"প্রকৃতিতে অতিরিক্ত ক্ষুধা বা পিপাসা নেই। প্রকৃতি অস্তেয় (অ-চুরি), অপরিগ (সম্পত্তির সাথে সম্পর্কহীন) এবং তৃষ্ণাহীন!" কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যা ঘটে তা মানুষের অতিরিক্ত ক্ষুধা-পিপাসার উন্মাদ প্রকাশ। প্রকৃতিকে ছিঁড়ে-নিংড়ে নিঃশেষ করার অবিবেচক উৎসব।
নিখুঁত সংসারী বা দূরদর্শী যেকোনো মানুষ কী করে? তারা বর্তমান উপার্জনের একটা ভাগ সরিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্য। ভবিষ্যৎ মানে কী? ভবিষ্যৎ মানে সন্তান, ভবিষ্যৎ মানে আরও একটু ভালো থাকার স্বপ্ন। হয়তো পাঁচ টাকা উপার্জন করলে দুটাকা সরিয়ে রাখে সংসারী মানুষ। নিজে একটু কম খেয়ে ভালো খাবারটা সন্তানের জন্য তুলে রাখে। সন্তানের জন্য একটা ভালো বাড়ি বানিয়ে রেখে যেতে চায়।
সেই একই নিখুঁত সংসারী মানুষটি প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে বিপরীত ভূমিকা রাখে! প্রাকৃতিক সম্পদ অসীম নয়, কিন্তু আমরা এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ করি যেন তার শেষ নেই! এখানে ভবিষ্যৎ ভাবনা কাজ করে না। এ ক্ষেত্রে আমরা দুটাকার সম্পদ ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে, সন্তানের ভাবনা ভেবে সরিয়ে রাখি না, প্রাকৃতিক সম্পদের অংশ নিজে একটু কম ভোগ করে সন্তানের জন্য তুলে রাখি না, পৃথিবীটাকে একটা বাসযোগ্য বাড়ি বানিয়ে রেখে যেতে চাই না।
ইতোমধ্যে আমরা—এই পৃথিবীর মানুষেরা ভাগ বসিয়েছি আমাদের সন্তানদের সম্পদে। তাতেই থামিনি, বলা যায় তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা।
এই বোধ যদি কারও ভেতরে কাজ করে, তবে তাকে প্রাকৃতিক কৃষির কাছে যেতে হবে। কেননা, প্রকৃতির যে অংশ নিয়েই কেউ ভাবুক না কেন, তাকে এই জায়গাতে গিয়ে ঠেকতে হবে, সে কী খাচ্ছে? তার প্রাণাধিক সন্তান কী খাচ্ছে? আর এই প্রশ্ন তাকে নিয়ে দাঁড় করাবে মনুষ্যকৃত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীর কাতারে।
'প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন' বইটি সেই ধারাবাহিক অপরাধগুলো এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়কে প্রামাণ্য বিশ্লেষণসহ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। বইয়ের মূল নামটি 'দ্য ফিলোসফি অব স্পিরিচ্যুয়াল ফার্মিং'। নামটি আমাদের ভাবনায় নাড়া দেয়। ফার্মিং ও স্পিরিচ্যুয়ালিটির সমন্বয় কীভাবে হলো?
এর জবাব বইতেই পাওয়া যাবে, "সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করার মানে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিধি-বিধানগুলো বিশ্বাস করা, সৃষ্টিকর্তার সংবিধানকে বিশ্বাস করা বা সৃষ্টিকর্তার ব্যবস্থাগুলোকে বিশ্বাস করা। প্রকৃতিই সৃষ্টিকর্তার ব্যবস্থা। প্রকৃতি যেসব বিধি-বিধান অনুসরণ করে, সেগুলোই সৃষ্টিকর্তার বিধান।"
বা "এই কৃষি ব্যবস্থা হচ্ছে প্রকৃতির একটি বিকশিত ও দৃশ্যমান রূপ, যাকে সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব কৃষি প্রযুক্তি বলা যায়।"
কিংবা "পূর্ণ ভক্তির সাথে প্রাকৃতিক কৃষি চর্চা করাই আধ্যাত্মিক কৃষি।" আরও একটু বিস্তারিত এভাবে বলা যেতে পারে, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী, সমুদ্র-নদী, বৃক্ষ-বায়ু ও ঋতু-পতঙ্গ সব কিছুর একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই ছন্দ পারস্পারিক, নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। মানুষও প্রকৃতিরই অংশ কিন্তু মানুষ এই ছন্দ থেকে, এই গতি থেকে ছিটকে গেছে।
প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন বলছে, "প্রকৃতি ও সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের আচরণবিধি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা।"
আধ্যাত্মিকতা ছাড়া প্রকৃতির ছন্দের সাথে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক কৃষি প্রকৃতির ছন্দেরই অংশ, যেখানে মাটিকে বুঝতে হয়, প্রকৃতিকে বুঝতে হয়, মাটিকে ভালোবাসতে হয়, নিবিড়ভাবে পাঠ করতে হয় এবং তাকে তার মতো করেই ফসল জন্মাতে দিতে হয়। এখানে জবরদস্তি খাটে না। একচ্ছত্র শাসক হয়ে ওঠার সুযোগ নেই।
বিপরীতে, সর্বব্যাপ্ত রাসায়নিক কৃষির ক্ষেত্রে জবরদস্তিই প্রথম এবং শেষ সত্য। জবরদস্তির উপকরণগুলো হলো, নানা রকম রাসায়নিক সার, কীটনাশক, হাইব্রিড, জিএমও বীজ। যেসব উপকরণের সাথে করে মানুষের জীবনে ঢুকে পড়েছে নানা রোগ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের একটি বড় কারণ রাসায়নিক কৃষি। প্রাকৃতিক কৃষির জন্য অপ্রাকৃতিক উপকরণগুলো প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি অনুসরণ করে সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব প্রযুক্তি।
প্রাকৃতিক কৃষি তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ জিরো বাজেট কৃষি। মাটিকে বাঁচাতে অথবা পুনরুদ্ধার করতে, সন্তানদের মুখের নিরাপদ আহার নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক কৃষিতে ফিরে যাওয়া বিকল্প পথ নেই। বিষযুক্ত খাবারের যে চক্রে আমরা ঢুকে পড়েছি সেখান থেকে সবাই বের হতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষার ভেতর থেকে আবার অর্গানিক কৃষি, জৈব কৃষিসহ আরও বিভিন্ন রকম কৃষি পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছে।
সুভাষ পালেকার দেখিয়েছেন সেগুলোও কেন প্রকৃতির রীতি অনুসারী নয়। "যা কিছু প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং যা কিছু প্রকৃতির ছন্দে চলে, তাই প্রাকৃতিক। যা প্রকৃতিতে নাই এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত, তাই হচ্ছে অপ্রাকৃতিক।" রাসায়নিক তাই অপ্রাকৃতিক।
জৈব সারকেও তাই তিনি বলেছেন রাসায়নিক। জৈব সার রূপে যে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করা হয়, তা প্রকৃতির ওপর এক রকম আরোপ করা। তাই সেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক সক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলার বদলে তাকে বিনাশ করে। লেখক প্রামাণ্য আলোচনায় দেখিয়েছেন জৈব কৃষি কীভাবে সবুজ বিপ্লবের চেয়েও অধিক শোষণমূলক। কাজেই রাসায়নিকের বিকল্প হিসেবে জৈব শব্দটি ব্যবহৃত হলেই নিরাপদ খাদ্য কিংবা কৃষকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।
আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রাকৃতিক কৃষি প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ফসল কি অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যের? প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন বইতে সেই জবাবও পাওয়া যাবে।
"আমরা যখন আধ্যাত্মিক কৃষির মাধ্যমে বিষমুক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করি, তখন আমরা শুধু খাদ্য উৎপাদন করি না; বরং আমরা প্রাকৃতিক খাদ্য রূপে প্রকৃত পুষ্টি এবং পরিপূর্ণ শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন করি।"
অর্থাৎ, যখন কেউ প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত বিষমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তখন তার ওষুধ নির্ভরতা বা কৃত্রিম চিকিৎসা খরচ কমে যায়। আর সেই বাড়তি খরচের কিছু অংশ ফসলের মূল্যের সাথে যুক্ত হলে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির দরজা উন্মুক্ত হয়।
প্রাকৃতিক কৃষি সম্পর্কে ধারণা পেতে মাঠে গিয়ে কৃষিকাজ করা আবশ্যক নয়। মাছ কোথায় থাকে এই নিয়ে বহুল প্রচলিত সেই কৌতুকটি বস্তুত সামগ্রিকভাবেই বাস্তব। সেই যে 'মাছ কোথায় থাকে'—শিক্ষকের করা এই প্রশ্নের উত্তরে এক শিশু বলেছিল, মাছ ফ্রিজে থাকে। সত্যিকার অর্থে আমাদের খাবার কোথায় থেকে, কীভাবে আসে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেকটা শিশুটির মতোই।
এই একটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রাকৃতিক কৃষির কাছে দাঁড়াতে হয়, আদি জ্ঞানের কাছে ফিরে যেতে হয়, খানিকটা হলেও আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে হয়।
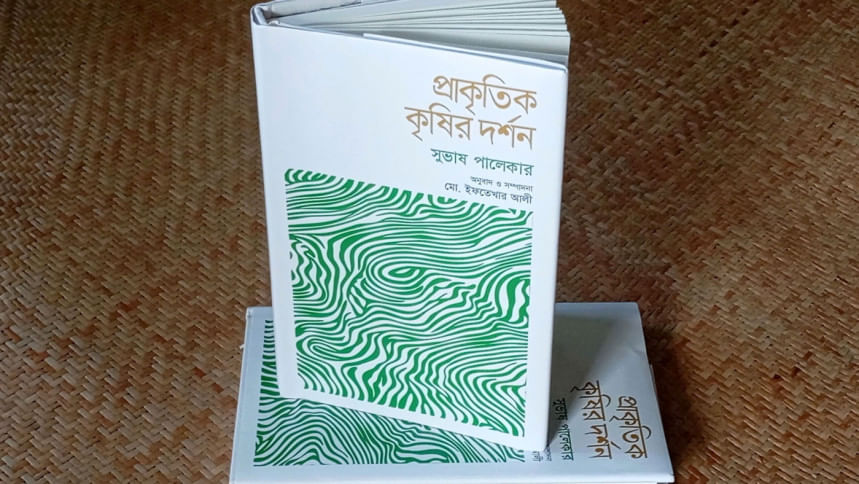



মন্তব্য
আপনার মতামত দিন
সাম্প্রতিক মন্তব্য
সাকিব আহমেদ
২ দিন আগেখুব গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক প্রতিফলন দেখা গেছে। ধন্যবাদ!